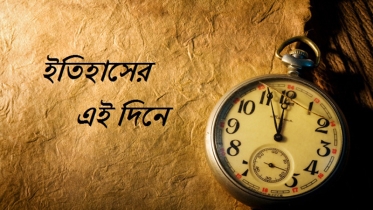(৫ অক্টোবরের পর)
আমার আব্বা আবু আহমদ আবদুল হাফিজের জন্ম হয় আমাদের পরিবারের সোনারপাড়ার পুরনো বাড়িতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন। আমার দাদি তার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯০৩ সালের ২৭ জুলাই তিনি কালাজ্বরে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা দেখেছি যে, আমার আব্বার সঙ্গে তার নানি চাঁদবিবির সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। এই বড় আম্মা ১৯৪৭ সালে প্রায় ৯৫ বছর বয়সে মারা যান। এছাড়া তার দাদি মতিবিবি সম্ভবত তার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন; সেই দাদিও ১৯০৬ সালের ৩১ জুলাই মারা যান। তার কিছুদিন পর ১৯০৬ সালে আমার দাদা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন সিলেট শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লাকড়িপাড়ার মোক্তার মুন্সী ইসরাইল আলীর কন্যা সৈয়দা বানুকে। এই দাদি জন্ম নেন ১৮৮৭ সালের ২৮ এপ্রিল এবং ১৯৫৫ সালের ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। আমার বাপ, চাচা, ফুপুরা মিলে তারা ছিলেন ছয় ভাই এবং দুই বোন। সবচেয়ে বড় বোন এবং আব্বার কথা ইতোমধ্যেই বলেছি। তার পরে ছিলেন পাঁচ ভাই এবং এক বোন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আবদুল মতিন পূর্ববাংলায় পানি এবং বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের পানি কমিশনার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আবদুল মালেক বলে আর এক ভাইয়ের জন্ম হয় ১৯১০ সালে। কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থায় ১৯২৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল গনি ছিলেন সারা পরিবারের সবচেয়ে বেশি মেধাবী। তিনি আইসিএস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) এবং আইএএএস (ইন্ডিয়ান অডিট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস্্ সার্ভিস) পরীক্ষা দেন এবং আইএএএস-এ পঞ্চম হওয়া সত্ত্বেও কোন চাকরি পেলেন না। আর ছিলেন অন্য বোন সাহেরা খাতুন। তার সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে, তিনি সিলেটে প্রথম মুসলিম মহিলা গ্র্যাজুয়েটের একজন ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি হন আমার শাশুড়ি। তার জন্ম হয় ১৯১৮ সালে এবং পরিণত বয়সে অর্থাৎ ২০০৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার পরে ছিলেন দুই ভাই আবদুল ওয়ারিস এবং আবদুল ওয়াসে। আবদুল ওয়ারিস দুটি সন্তান রেখে ৩৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ১৯৬১ সালে। আবদুল ওয়াসে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ সালে মারা যান।
আমার দাদা আসাম সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন বলে তাকে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় বাস করতে হয়। তিনি ১৯০৮ সালে তার বড় ছেলে আমার আব্বাকে সিলেটে যাতে তিনি পড়াশোনা করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করেন। বাড়িতে তখন তার অভিভাবক হন তার চাচা আবদুর রশিদ। একইসঙ্গে তিনি ১৯০৮ সালে আব্বার জন্য আর একজন অভিভাবক ঠিক করে দেন। সিলেট সরকারি বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক আবদুল গফুর চৌধুরী ঐ সময় কলেজে পড়াশোনার জন্য গোলাপগঞ্জ থেকে সিলেটে আসেন। তাকে আমার দাদা তার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেন যে, তিনি তার বড় ছেলের দেখাশোনা করবেন। আমার দাদার তখন কোন দ্বিতীয় সন্তান হয়নি। আবদুল গফুর সাহেব সিলেট থেকে বিএ পাস করে আসামের শিক্ষা বিভাগে চাকরি নেন এবং সিলেটেই অবস্থান করতে থাকেন। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন আব্বার দ্বিতীয় অভিভাবক। আব্বা ১৯১৭ সালে সিলেট সরকারি বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। তাদের পরীক্ষা দেয়াটা বেশ জটিল ছিল। সেবার তিনবার পরীক্ষার তারিখ বদলাতে হয়। কারণ, তিনবারই কোন না কোন প্রশ্নপত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। আব্বা মুরারীচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। তখন কলেজটি সিলেটের চৌহাট্টায় অবস্থিত ছিল। তার যখন বিএ পরীক্ষা দেয়ার কথা সেই সময় দেশে খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগে। ১৯২১ সালে আব্বা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তার বড় মামা আবদুল হামিদ (তিনি ১৯১২ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাস করে ১৯১৫ সালে কলকাতা থেকে আইন পাস করেন এবং তার পরেই সিলেট জেলা বারে যোগদান করেন; তখন তিনি ছিলেন এই বারের একমাত্র মুসলমান আইনজীবী)। তিনি ১৯২৩ সালে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বারবার নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হন এবং ১৯২৯ সালে হন প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী। এই পদে তিনি বহাল থাকেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু ভোটে পরাজিত হন। তিনি কিছুদিন সিলেটে অবস্থান করার পর ১৯৪২ সালে কলকাতা চলে যান এবং ১৯৪৫ সালে সিলেটে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে আসামে মুসলিম লীগ দলের ডেপুটি লিডার হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে তিনি পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও সমবায়মন্ত্রী হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন এবং ঢাকার র্যাংকিন স্ট্রিটে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৪ সালের ১৩ জুন তিনি পরলোকগমন করেন।
আমার আব্বা তার এই মামার ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই তিনি ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। আমার দাদা তখন আসামের নওগাঁও জেলায় ইএসি (এক্সট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার) ছিলেন। তিনি আব্বার এই আচরণে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তাকে তিনি নওগাঁও ডেকে পাঠালেন। নওগাঁও পৌঁছার পরেই তিনি তাকে রাজশাহীতে পাঠিয়ে দিলেন। রাজশাহীতে তখন তার এক মামা (মায়ের চাচাতো ভাই) মৌলবী আবদুল হাকিম রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আব্বা রাজশাহীতে পৌঁছার পর তার মামা তাকে রাজশাহী কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেখান থেকে ১৯২২ সালে বিএ পাস করে তিনি কলকাতা চলে গেলেন। ১৯২২-২৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতায় কারমাইকেল হোস্টেলে থাকেন এবং সেখান থেকে ১৯২৪ সালে আরবিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এমএ পাস করেন ও ১৯২৬ সালে আইন পাস করেন। কলকাতায় থাকতে তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনের ছাত্র বিভাগের সম্পাদক ছিলেন এবং তখনকার দিনে সিলেটের যেসব ছাত্র কলকাতায় যেতেন তাদের তিনি অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিলেট জেলা বারে যোগদান করেন। তার সারাজীবনে আইন ছাড়া আরও দু/তিনটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি লেখাপড়ার বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং ১৯৩১ সালে বখতিয়ার বিবি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। শুরু থেকে পঁয়ত্রিশ বছর এই স্কুল কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং পরবর্তী চৌদ্দ বছর ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। ১৯৩৯ সালে যখন সিলেটে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি তারও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র মুসলমান সদস্য। ১৯৩৩ সালে পাঁচ বছরের জন্য তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। ১৯৫০ সালে তিনি ছিলেন সিলেটের কাজী জালাল উদ্দীন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন কলেজে খ-কালীন শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময়ে শিক্ষকের অভাবে মহিলা কলেজ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম এবং মদনমোহন কলেজেরও কিছু অসুবিধা হয়। এই দুটি কলেজেই তিনি কিছু সময় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫১ সালে পাঁচ বছরের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টেরও সদস্য ছিলেন। সবশেষে ১৯৬৮ সালে তিনি সিলেট আইন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮১ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য তাকে বয়সের কারণে আইন কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছাড়তে হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ নির্দেশে বৃদ্ধ বয়সেও তাকে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতে দেয়া হয়। আমার মনে হয়, তার জীবনে এই দায়িত্বটিকেই তিনি সবচেয়ে উত্তম বলে বিবেচনা করতেন।
আমার আব্বার দ্বিতীয় আগ্রহ ছিল রাজনীতি। ছাত্র বয়সেই তিনি সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন এবং এই কারণেই তিনি এক বছর বিএ পরীক্ষা দিতে বিরত থাকেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের একটি ডাক ছিল ব্রিটিশ শিক্ষা বর্জন, যদিও এই আহ্বানে খেলাফত নেতারা একমত ছিলেন না। সিলেট বার লাইব্রেরিতে যোগদানের পর তিনি বেশ কিছুদিন ইসলাম মিশনের পক্ষে কাজ করেন। রাজনীতিতে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন তার মামার কারণে এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচন থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে তিনি তার মামার মুখ্য এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তাকে সক্রিয় করে তোলেন সিলেটের আর এক কৃতী রাজনীতিবিদ ভাদেশ্বরের আবদুল মতিন চৌধুরী। আবদুল মতিন চৌধুরী আজীবন মুসলিম লীগের কর্মী ও নেতা ছিলেন। আসামে মুসলিম লীগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহকে মুসলিম লীগের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। তিনি আসামে সাদুল্লা মন্ত্রিসভায় এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিলেটে তিনি ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং আমার আব্বাকে এই ব্যাপারে সিলেট জেলার দায়িত্ব প্রদান করেন। আব্বা ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সে সময় সভাপতি ছিলেন টুকেরবাজারের আবদুর রশিদ। পরবর্তীকালে তিনি ১৯৪৭ সালে সিলেট মুসলিম লীগ গণভোট বোর্ডের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-ভারত যখন ভারত ও পাকিস্তানে ভাগ হলো তখন বঙ্গদেশেরও ভাগ হয়। এই ভাগাভাগিতে ঠিক হয় যে, পূর্ববাংলা যা হবে পাকিস্তানের এলাকা, সেখানে আসাম প্রদেশের সিলেট যুক্ত হতে পারে যদি সেখানে গণভোটে সেইরকম রায় পাওয়া যায়। গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ৬ ও ৭ মাার্চে এবং তাতে রায়টি হয় পাকিস্তানের পক্ষে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন বিশেষ আদেশে প্রতিষ্ঠিত নগর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক। অতঃপর রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কমে যায় এবং তিনি শিক্ষা খাতে ও সমাজসেবায় অধিক সময় ব্যয় করতে থাকেন। সিলেটে এমন কোন সামাজিক উদ্যোগ ছিল না যেখানে তিনি সক্রিয়ভাবে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেননি। সিলেটে ১৯৪০ সালে একটি মুসলিম হল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। তারই ফসল হয় বর্তমানের শহীদ সুলেমান হল। এই হল কমিটির টানা সাত বছর ধরে তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং তার নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার সময়েই তিনি পদত্যাগ করে ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমানকে এই দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলার সমর্থক ছিলেন এবং আগেই বলেছি যে, বায়ান্নোতে এই আন্দোলনের সময় তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সিলেটে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম মহিলা লীগ এবং তমদ্দুন মজলিশ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আব্বার মতো কতিপয় মুসলিম লীগ নেতা এই আন্দোলনে সমর্থন দেয়ায় আন্দোলনটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার আর একটি আগ্রহের বিষয় ছিল সমবায় আন্দোলন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই ১৯২৭ সালে তিনি সিলেট কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হন এবং ১৯৫০ সালে এই সমবায় ব্যাংকের সভাপতি হন। ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট কো-অপারেটিভ এ্যাডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন পদাধিকারবলে জেলা প্রশাসক। এই সোসাইটি বর্তমানে প্রসিদ্ধ ব্লু-বার্ড স্কুল প্রতিষ্ঠায় মূল্যবান অবদান রাখে। তিনি ১৯৬১ সালে সিলেট জেলা বারের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং কয়েকবারই এই বারের সভাপতি ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ দু’বারই জেলা বারের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৬ সালে সিলেট জেলা বার তার এবং আরও কয়েকজনের আইনজীবী হিসেবে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। তখন থেকেই আইনজীবীদের পঞ্চাশ বছরের পেশাকে স্বীকৃতি দেয়ার একটি নিয়মিত ব্যবস্থা এই জেলা বারে প্রতিষ্ঠা পায়।
আমার আব্বার সবচেয়ে বড় সম্পদটি ছিল, একটা অত্যন্ত আধুনিক মন এবং যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও গভীর আগ্রহ। শেষ বয়সে তিনি যে কোন ধরনের বই পেলেই সেটা পড়তেন। আমার সঙ্গে তিনি কিছুদিন রাওয়ালপিন্ডিতে ছিলেন এবং ঢাকায় তো প্রায়ই থাকতেন। আমার বাড়িতে তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল নাতি-নাতনি ছাড়া আমার গ্রন্থ সংগ্রহ। হঠাৎ হঠাৎ তিনি কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে যেতেন। একবার যেমন তিনি জন্মরহস্য ও বিজ্ঞানে খুব পড়াশোনা শুরু করে দিলেন। অবশ্য ইতিহাস ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় এবং তার অধ্যাপনার বেশিরভাগই ছিল ইতিহাস বিষয়ে। সেখানে শুধু ভারতবর্ষ এবং ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল না। তিনি ইউরোপের ইতিহাস, আধুনিক ইতিহাস এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসও পড়াশোনা করতেন। ১৯৮৫ সালে তার পঁচাশি বছর পূরণ হওয়ার সামান্য আগে ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি সিলেটে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তার তেমন কোন অসুখ-বিসুখ ছিল না। জানুয়ারি মাসের কোন এক সময়ে তিনি বাথরুমে পড়ে গিয়ে সামান্য আহত হয়ে শয্যাশায়ী হন (অবশ্য কোন হাড় ভাঙ্গেনি)। এই সময়ই আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু হয়। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন তার কোন সন্তান-সন্ততি (আমরা তখন বারোজন ছিলাম) কেউই উপস্থিত ছিল না। তবে তার শ্যালিকা শামসুন্নেসা বেগম (হাওয়া খালা), শ্যালক ডা. সৈয়দ শাহ আনোয়ার এবং তার দুই নাতনি, বড় মেয়ের দুই মেয়ে নমু ও ইলোরা এবং নাতজামাই ডা. একেএম হাফিজ সে সময় তার পাশে ছিলেন।
চলবে...